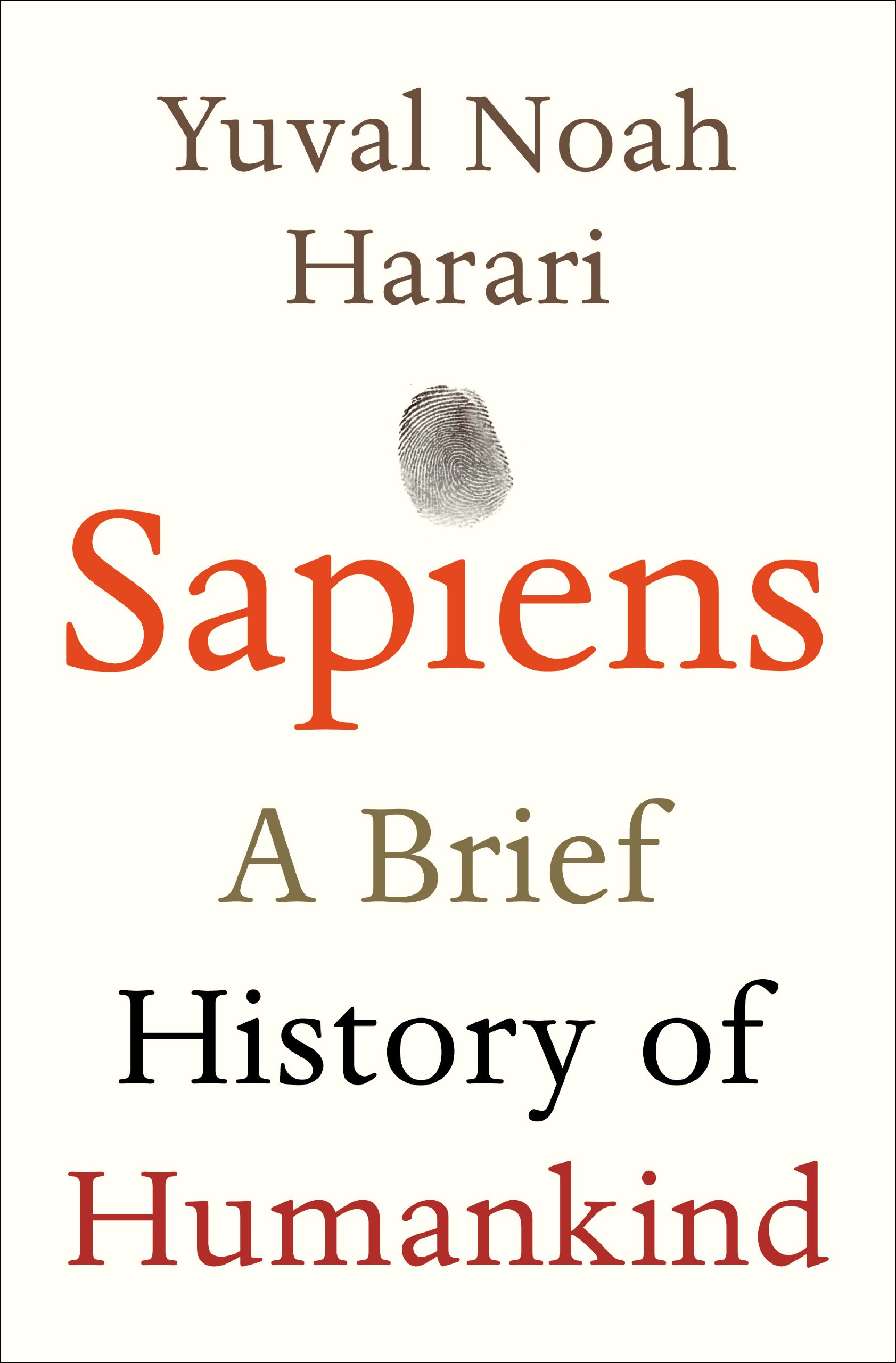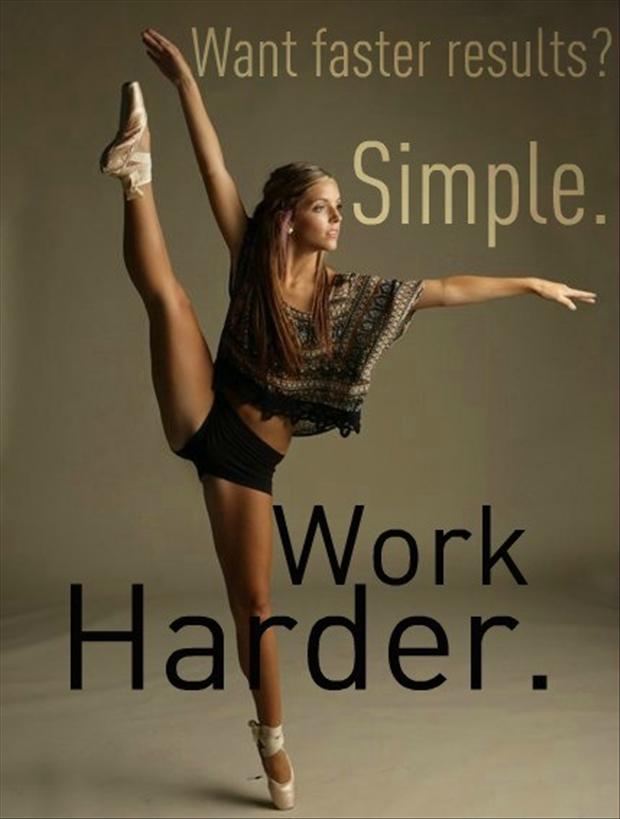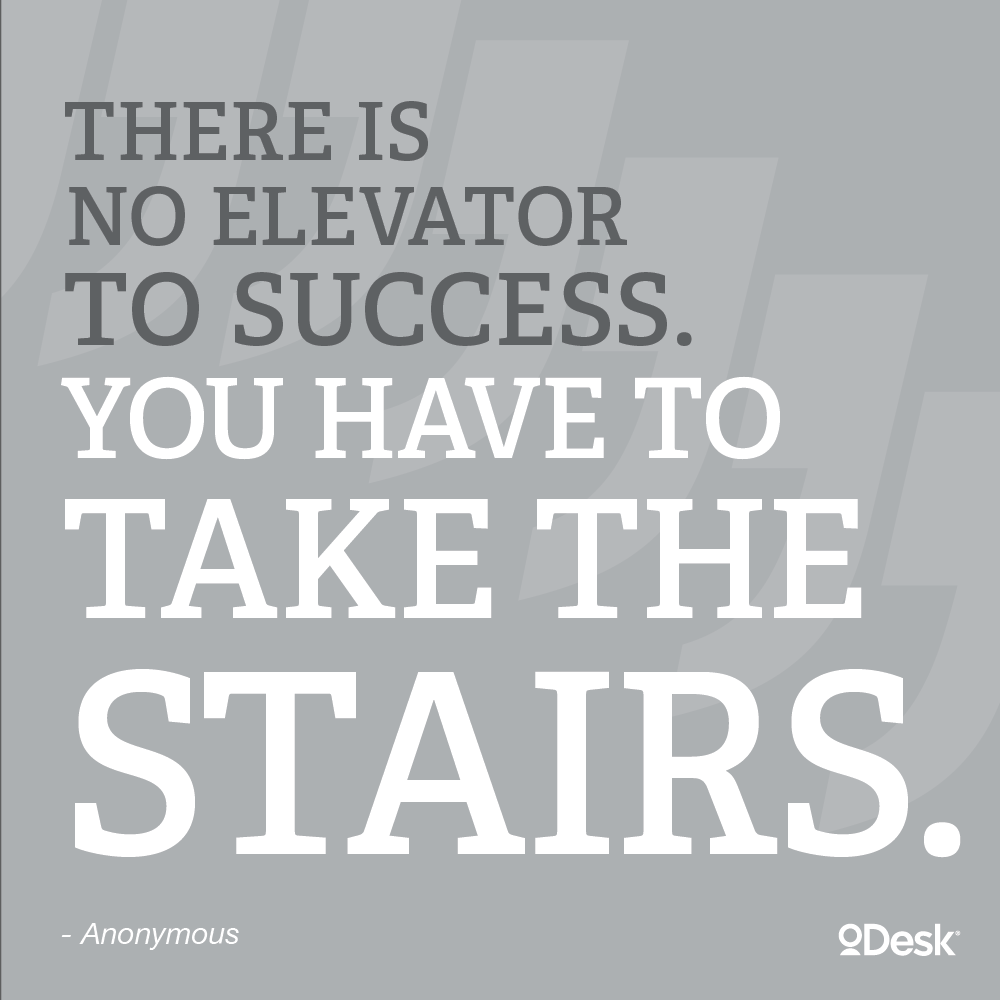১।
গত অক্টোবরের ৭ তারিখে হামাসের ইজরায়েলের অভ্যন্তরে হামলায় প্রায় ১২০০ মানুষ মারা যাওয়ার পর ইজরায়েল ফিলিস্তনের উপর ক্রমাগত বোমাবর্ষন এবং স্থল অভিযান পরিচালনা শুরু করে। ইজরায়েলের হামলায় এখন পর্যন্ত প্রায় ২১,০০০ এর বেশি ফিলিস্তিনি মানুষ মারা যায় যার বেশিরভাগই নারী এবং শিশু।
ইজরায়েল (এবং তাদের সবচেয়ে বড় সমর্থক রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্র) হামাসকে একটা সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করে। তাই হামাসের ৭ই অক্টোবরের হামলাকে একটা সন্ত্রাসী হামলা হিসেবে চিহ্নিত করে তারা এখন হামাসকে নির্মুল করার অভিযান পরিচালনা করছে। হামাসকে নির্মুল করার নামে ইজরায়েল এখন ফিলিস্তিনিদেরকে এক প্রকার জাতিগত নিধন করছে গাজা এলাকা থেকে।
পুরো মধ্যপ্রাচ্যে একমাত্র ইরান আর ইয়েমেনের হুতিরা হামাস এবং ফিলিস্তিনের পক্ষে সরাসরি কথা বলছে। হুতিরা নিজেরাই তেমন একটা শক্ত না, তার উপর সৌদি আরব গত ৮/৯ বছর ধরে হুতিদেরকে ক্রমাগত বোমা মেরে প্রায় ধ্বংস করে দিয়েছে। এরপরও ওরা ওদের যা আছে তাই নিয়ে আমেরিকা এবং ইউরোপের মতো পরাশক্তিদের চ্যালেঞ্জ দিয়ে লোহিত সাগরে ইজরায়েলমুখী সব জাহাজ চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে।
তুরস্কের এরদোগান মাঝে মাঝে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে দুই একটা হম্বি তম্বি বক্তৃতা দিয়েই ফিলিস্তিনের প্রতি তার সমর্থন প্রকাশ শেষ করেন। ইজরায়েলে যাওয়া তেলের একটা বড় অংশ যায় তুরস্কের মধ্য দিয়ে। এবং ইজরায়েলের তেলের সবচেয়ে বড় উৎস হচ্ছে মুসলিম দেশগুলো।
সৌদি আরব আর আরব আমিরাত প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে ইজরায়েল আর আমেরিকার বন্ধু।
মিশর প্রতি বছর আমেরিকা থেকে শত শত মিলিয়ন ডলারের সামরিক সহায়তা পেয়ে থাকে এক ধরণের ঘুষ হিসেবে। এই ঘুষের বিনিময়ে মিশর ইজরায়েলের সাথে বন্ধুত্ব বজায় রাখে আর মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার চামচামি করে থাকে।
লেবানন এবং জর্ডান ইজারায়েলের সীমান্তবর্তী দুই দেশ। দুই দেশই ফিলিস্তিনের প্রতি সহানুভূতিশীল, কিন্তু দুটি দেশই সামরিকভাবে দুর্বল, তাই তারা কোনভাবেই ইজরায়েলের সাথে লড়তে যাবে না।
তো এ ধরণের একটা অবস্থায় ফিলিস্তিনের মতো একটা পরাধীন দেশ, যাদের সবকিছু ইজরায়েল নিয়ন্ত্রণ করে, তারা কীভাবে লড়াই করবে ইজরায়েল সাথে? ইজরায়েল প্রায় পোড়ামাটি নীতি অনুসরণ করে অসহায় ফিলিস্তিনিদের নির্মুল করে দিচ্ছে।
২।
এমন না যে আরব রাষ্ট্রগুলো কখনো ইজরায়েলকে মোকাবেলা করার চেষ্টা করেনি। ইজরায়লের জন্ম থেকে বেশ কয়েকবার আরব রাষ্ট্রগুলোর সাথেক ইজরায়েলের যুদ্ধ হয়েছিল। প্রতিটি যুদ্ধে ক্ষুদ্র ইজরায়েল আক্রমণকারী সব আরব রাষ্ট্রগুলোকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। ইজরায়েল আরব রাষ্ট্রগুলোকে শুধু পরাজিত করেই ক্ষান্ত হয়নি, মিশরের বিশাল সিনাই অঞ্চল এবং সিরিয়ার গোলান উপত্যকাও দখল করে নেয় তখন।
১৯৪৮ সালে ইজরায়েল এর জন্মের পরপরই মিশর, সিরিয়া, ইরাক, জর্ডান, লেবানন, এবং সৌদি আরব (মিশরের কমান্ডের অধীনে) ইজরায়েলকে আক্রমণ করে। এই যুদ্ধের পর ইজরায়েল ফিলিস্তিনের আরো অনেক এলাকা দখল করে নেয়।
এরপর থেকে আরো অনেকবার আরব দেশগুলোর সাথে ইজরায়েলের যুদ্ধ হয়, এবং প্রতিটি যুদ্ধে ইজরায়েল জিতে যায়।
এরপর অনেকগুলো দেশ, যেমন মিশর, জর্ডান, তুরস্ক, এবং সম্প্রতি আরব আমিরাত ইজরায়েলকে মেনে নেয় এবং তাদের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে।
৩।
আমরা মুসলমানরা নামাজের পর মুসলিম “উম্মাহ”‘র জন্যে দোয়া করি, সারা বিশ্বের মুসলমানদের সমৃদ্ধির জন্যে দোয়া করি। কিন্তু সারা বিশ্বের মুসলমানদের প্রকৃত অবস্থাটা আসলে কেমন?
সৌদি আরবের সৌদ বংশ শত বছর ধরে রাজত্ব করে চলছে। মানুষের কোন মতো প্রকাশের অধিকার নাই, নিজের মতো কথা বলা বা লেখার অধিকার নাই, নিজের ইচ্ছে মতো কাপড় চোপড় পরার অধিকার নাই। কয়েকদিন আগ পর্যন্তও মেয়েরা গাড়ি চালাতে পারতোনা। রাজা এবং রাজপুত্রদের শত শত পত্নী এবং উপ-পত্নী আছে।
ইরানের শাসন হচ্ছে কাঠ মোল্লাদের হাতে। সেখানে নৈতিক পুলিশ নামে একধরণের পুলিশ বাহিনী আছে যারা মেয়েদের কাপড় চোপড় পরা পছন্দ না হলে ধরে নিয়ে যায়, এবং কখনো কখনো অত্যাচার করে মেরে ফেলে।
আফগানিস্তান, ইরাক, সিরিয়া, সোমালিয়া, লেবানন, লিবিয়া, সুদান, আর্মেনিয়া, আজারবাইজান সহ অসংখ্য মুসলিম দেশে প্রায় নিয়মিত যুদ্ধ চলছে – হয় নিজেদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ কিংবা প্রতিবেশী মুসলিম দেশের সাথে যুদ্ধ।
বাংলাদেশ, পাকিস্তান, তুরস্ক, মিশরের মতো দেশগুলোতে গণতন্ত্রের নামে চলছে হয় স্বৈরতন্ত্র, কিংবা সামরিক বাহিনীর পরোক্ষ শাসন।
একটা মুসলিম দেশও একটা সমৃদ্ধ এবং শক্তিশালী দেশ হিসেবে বিশ্ব মঞ্চে আবির্ভুত হতে পারেনি।
৪।
কয়েক মাস আগে লিঙ্কডইনে দেখেছিলাম একটা বাংলাদেশী ছেলে লিখেছে তার ইচ্ছা যে সে ফিলিস্তিন যেয়ে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। এতে যদি সে মরেও যায় তাতেও সে খুশি – একটা মহৎ কাজ করেতে যেয়ে সে জীবন দিয়েছে!
আমার ধারণা শুধু বাংলাদেশ নয়, অনেক মুসলিম দেশের অনেক তরুণের এই ইচ্ছা এবং স্বপ্ন। ফিলিস্তিনিদের প্রতি যে অবিচার, নির্যাতন, আর নিধন হচ্ছে এর জন্যে এ ধরণের ইচ্ছা থাকা খুব একটা অবাক হওয়ার মতো কিছু নয়।
কিন্তু এই তরুণেরা ফিলিস্তিনে যেয়ে ইজরায়েলের ঠিক কী করবে? ইজরায়েলের আছে পৃথিবীর সবচেয়ে আধুনিক পঞ্চম প্রজন্মের যুদ্ধ বিমান, সর্বাধুনিক আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, পারমানবিক বোমা, সাবমেরিন, ইত্যাদি ইত্যাদি। আর আছে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রের নিঃশর্ত এবং সর্বাত্মক সহযোগিতা। আমাদের ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-চট্রগ্রামের একটা ছেলে যেয়ে সেই এফ-১৬/৩৫ যুদ্ধ বিমানের বিরুদ্ধে ঠিক কী করতে পারবে?
আজকে যদি তলোয়ার দিয়ে যুদ্ধ হতো, তাহলে হয়তো আমরা বখতিয়ার খলজির উদাহরণ দিতে পারতাম। কিংবা ইসলামের প্রারম্ভিক যুগের ঈমানি জোশে জিতে যাওয়া যুদ্ধের কথা বলতে পারতাম। কিন্তু বর্তমান যুগে ইমানি জোশে যুদ্ধে জেতার কোন সুযোগ নাই। নেভাদার মরুভূমিতে আমেরিকার বিমান ঘাঁটিতে বসে এক বোতাম টিপে দশ হাজার মাইল দুরের কোন এক জায়গায় ড্রোন থেকে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে নিমিষেই একদল মানুষকে মেরে ফেলা যায়। এই সেদিন ইজরায়েল ইরানের এক ব্রিগেডিয়ার জেনারেলকে সিরিয়ায় মেরে ফেলল বিমান থেকে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা করে!
বাংলাদেশের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেপেলেরা ক্যাম্পাসে রাজনীতির নাম করে চাঁদাবাজি করে; রামদা, পাইপ গান, বা কাটা রাইফেল নিয়ে প্রতিপক্ষকে মেরে কেটে জখম করে দেয়। এরা ফিলিস্তিনের প্রতি অবিচার দেখে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিপ্লব সাধন করে ফেলতে পারে, কিন্তু বাস্তবে চাঁদাবাজির টাকার ভাগ পাওয়া কিংবা নেতার মাধ্যমে কিছু অন্যায্য সুযোগ সুবিধা পাওয়ার বাইরে এদের আসলে কোন ক্ষমতাই নাই।
এমনকি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ইজরায়েলের প্রোপাগান্ডার জবাব দেয়ার মতো জ্ঞান বা পড়ালেখা বাংলাদেশ এবং অনেক মুসলিম দেশের ছেলেপেলের নাই।
ফিলিস্তিনের অনেক তরুণেরা চট্রগ্রামের ভাটিয়ারীর বাংলাদেশ মিলিটারি একডেমি থেকে কমিশন্ড অফিসার হয়ে যায়। কিন্তু তাতে যে কিছু লাভ হচ্ছে না সেটা তো তাদের বর্তমান অবস্থা দেখলেই বোঝা যায়।
কিন্তু চিন্তা করে দেখুন। বাংলাদেশের হাসিনা এবং খালেদারা একে অপরের সাথে ঝগড়া করার পাশাপাশি দেশটাকে একটা চমৎকার উন্নত/ধনী গণতান্ত্রিক দেশে পরিণত করতো, বাংলাদেশের যদি একটা শক্তিশালী মিলিটারি থাকতো, বাংলাদেশের ডিজিএফআই/এনএসআই যদি সরকার বিরোধীদের পেঁদানিতে ওস্তাদ হওয়ার বাইরে গিয়ে একটা শক্ত চৌকস গোয়েন্দা বাহিনী হতে পারতো, তাহলে আমরা আজকে সত্যিকার অর্থে ফিলিস্তিনকে সাহায্য করতে পারতাম!
সৌদি আরবের রাজা-বাদশাহরা যদি আজকে নিজের গদি এবং শত শত পত্নী/উপপত্নী রক্ষার চেয়ে দেশকে ধনী ও শক্তিশালী করার চেষ্টা করতো তাহলে তারাও আজকে আমেরিকার রক্ত চক্ষু উপেক্ষা করে ফিলিস্তিনকে সাহায্য করতে পারতো।
একই অবস্থা কমবেশি সব মুসলিম রাষ্ট্রের।
ইরানের কাঠ মোল্লারা হুঙ্কার ছাড়তে ওস্তাদ। কিন্তু সত্যিকারের যুদ্ধক্ষেত্রে তাদেরকে মোটামুটি কখনোই পাওয়া যায় না। বাংলাদেশে যেমন পুলিশ-মিলিটারি সরকার বিরোধীদের পেঁদানিতে ওস্তাদ, ইরানেও সেখানকার পুলিশ- মিলিটারি সাধারণ মানুষদের ধরে ধরে পেটাতে ওস্তাদ। বাংলাদেশের মিলিটারি যেমন মিয়ানমারের মতো একটা দরিদ্র্য দেশের মিলিটারিরও একটা কেশ ছিঁড়তে পারে না (তারা আট লাখ রোহিঙ্গাদের ধুম করে বাংলাদেশে ঠেলে দেয়ার পর), কিন্তু সাধারণ মানুষদের ধরে নিয়ে যেয়ে পিটিয়ে ভর্তা বানিয়ে দিতে খুবই পারদর্শী (অপারেশন ক্লিন হার্ট, র্যাব/ডিজিএফআই কর্তৃক উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া), ইরানের মিলিটারিও তেমনি তাদের বড় বড় অফিসারদেরকে আমেরিকা এবং ইজরায়েল ড্রোন বা যুদ্ধ বিমান দিয়ে মেরে ফেললেও আমেরিকা বা ইজরায়েলের একটা কেশও ছিঁড়তে পারে না।
তুরস্ক মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উন্নত ও ধনী। কিন্তু আমেরিকা বা ইজরায়েলের বেলায় আসলে তাদের সব কিছু হম্বি তম্বির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। গাজাকে ধ্বংস্তুপে পরিণত করার সময় তুরস্কের প্রেসিডেন্ট শুধু কথার সমালোচনা করেই দায়িত্ব শেষ করেছেন।
মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে একমাত্র পাকিস্তানের পারমানবিক বোমা আছে। পাকিস্তানের অর্জনের মধ্যে মনে হয় এই একটা জিনিসই আছে শুধু। তাছাড়া দেশটা আসলে একটা অর্ধমৃত দেশ। পাকিস্তানের মিলিটারি আর মোল্লারা মিলে দেশটাকে একটা নরক বানিয়ে রেখেছে। তারা কিভাবে অন্য আরেকটা দেশকে সাহায্য করবে?
৫।
আমেরিকা, ইজরায়েল, বা অন্যান্য ঔপনিবেশিক শক্তিগুলোর হাত থেকে বাঁচতে হলে সন্ত্রাসী হামলা করে সাধারণ মানুষদেরকে মেরে কোন লাভ হবে না। বিন লাদেন এর আল কায়েদা, ইরাকের আইসিস, বা আফগানিস্তানের তালেবানের মতো সন্ত্রাসী এবং বর্বর সংগঠন করে নিজ দেশের মুসলমানদের এবং বিদেশের সাধারণ মানুষদেরকে বোমা মেরে বা কল্লা কেটে আমেরিকা বা ইজরায়েলের একটা কেশও ছেঁড়া যাবে না।
ইজরায়েল (এবং তাদের প্রিয়তম বন্ধু আমেরিকার) কাছ থেকে ফিলিস্তিনকে বাঁচাতে হলে মুসলিম দেশগুলোকে পড়ালেখা করতে হবে। মানুষের প্রতি, মানুষের জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা সম্পন্ন একটা জ্ঞান-ভিত্তিক সমাজ গড়ে তুলতে হবে। ভিন্ন মত ও পথের প্রতি সহনশীল হতে হবে।
স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলেয়েমেদের পড়ালেখার পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে পড়ালেখার পাশাপাশি গবেষণা করার ব্যবস্থা করতে হবে।
আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণাগারগুলোতে অত্যাধুনিক যুদ্ধ বিমান, ক্ষেপণাস্ত্র, আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, যুদ্ধ জাহাজ, সাবমেরিন, স্যাটেলাইট, ড্রোন, ইত্যাদি বানানোর গবেষণা করতে হবে। এবং দেশের ভেতরেই এগুলো বানানোর ব্যবস্থা করতে হবে। এরপর আমাদের মিলিটারি যখন বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী মিলিটারি হয়ে দাঁড়াবে তখন তারা দেশের মানুষকে বাঁচানোর শপথ নিয়ে কাজ করবে, তাদেরকে ধরে নিয়ে পেঁদানি দিতে নয়। সেই শক্তিশালী মিলিটারি তখন আমেরিকা বা ইজরায়েল বা অন্য যে কোন ঔপনিবেশিক বা দুর্বৃত্ত রাষ্ট্রের অপকর্মের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়ার জন্যে সব সময় প্রস্তুত থাকবে। মিয়ানমার এর মতো গরীব, পুঁচকে একটা দেশ আট লাখ মানুষকে আমাদের দেশের দিকে ঠেলে দেয়ার চিন্তা করার আগে নিজদের প্যান্ট ভিজিয়ে ফেলবে পরিণতির কথা চিন্তা করে।
আমাদেরকে জেনেটিক্স এবং বায়ো টেকনোলজি নিয়ে গবেষণা করতে হবে। অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা করতে হবে।
মানুষের কথা বলার স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। মানুষের লেখার স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। মানুষের চিন্তার স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। মানুষের নিজের পছন্দের কাপড় চোপড় পরার স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। মানুষের নিজস্ব ধর্ম বিশ্বাস এর স্বাধীনতা নিশ্চিত করেতে হবে। কে কী বিশ্বাস করবে, কে কোন ধর্মালয়ে যাবে, কে কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যাবে, সেটা একান্তই ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভর করবে। আমার পছন্দ-অপছন্দ কিংবা বিশ্বাস আমি অন্যের উপর চাপিয়ে দিতে পারবোনা।
লিঙ্কডইনে ফিলিস্তিনের পক্ষে যুদ্ধে করতে যেতে চাওয়া ছেলেটি ফিলিস্তিনকে অনেক বেশি সাহায্য করতে পারতো যদি সে আজকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্যে আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র বানাতে পারতো!
বাংলাদেশের ফেইসবুকে ফিলিস্তিনের পক্ষে বিপ্লব করা প্রত্যেকেই অনেক বেশি ফিলিস্তিনকে সাহায্য করতে পারতো যদি এরা সবাই মিলে বাংলদেশকে পৃথিবীর অন্যতম ধনী এবং শক্তিশালী দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পারতো।
আর একটা ধনী এবং শক্তিশালী দেশ হওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা এবং গবেষণার পরিবেশ নিশ্চিত করা, মানুষের মত ও পথের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা, এবং শত রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সাংস্কৃতিক পার্থক্য থাকা সত্বেও অন্য মানুষদের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা থাকতে হবে।
অন্যের মত ও পথের প্রতি আমরা যে কী পরিমাণ অসহিষ্ণু সেটা নিয়ে আরেকদিন আরো বিশদভাবে লেখার ইচ্ছা আছে। কিন্তু এখানে শুধু এটাই বলতে চাই যে মানুষ যদি নিজের মতো করে চিন্তা করতে না পারে, নিজের মতো করে কথা বলতে না পারে, নিজের মতো করে কাজ না করতে পারে, নিজের পছন্দের কাপড় চোপড় পরে না পারে, যদি অন্য লোকের কথার ভয়ে থাকতে হয়, যদি পুলিশ-মিলিটারির ভয়ে একটা ভয়ের জীবন যাপন করে কাটিয়ে দিতে হয় পুরো জীবন, তাহলে সেই সমাজ বা দেশ কোনদিন একটা সমৃদ্ধশালী দেশে পরিণত হতে পারবে না।
আর নিজেরা ধ্বজভঙ্গ হয়ে থেকে অন্য দেশকে সাহায্য করার তো প্রশ্নই উঠে না।
৬।
ফিলিস্তিনের দুর্ভাগ্য। সারা দুনিয়ার মানুষে চোখের সামনে দিয়ে তাদেরকে একরকম নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হচ্ছে। যারা তাদেরকে নিয়ে সবচেয়ে বেশি চিন্তিত এবং সমব্যথিত – মূলত সব মুসলমান প্রধান দেশগুলো – তারা প্রায় সবাই-ই এক ধরণের স্বেচ্ছা ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান বিবর্জিত, মানুষের প্রতি, জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা সম্মানহীন এক সমাজ ব্যবস্থায় নিজেদের সাথে নিজেরা ঝগড়া-ঝাঁটি মারামারি করে এক প্রকার অর্ধমৃত জীবন যাপন করে যাচ্ছে।